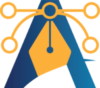অধ্যায় এক
লগ এন্ট্রিঃ সোল ৬
বাঁশ খেয়ে গেছি আমি।
এছাড়া আর কী বলব!
আছোলা বাঁশ।
জীবনের সেরা দুটো মাসের ষষ্ঠ দিন আজ, ভালো কাটার বদলে পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নে।
জানি না এই রিপোর্ট কেউ পড়বে কি না। হয়তো পড়বে, আজ থেকে একশো বছর পর।
রেকর্ডে থাকার জন্য বলছি… সোল ৬-এ মরিনি আমি। তবে বাকি ক্রু-রা সম্ভবত তাই ভেবেছে। ওদের দোষ দিচ্ছি না। হয়তো আমার জন্য জাতীয় শোকদিবস হিসেবে পালন করা হবে একটা দিন, আর উইকিপিডিয়া পেইজে লেখা থাকবে- মার্ক ওয়াটনি হচ্ছে মঙ্গলে মারা যাওয়া একমাত্র মানুষ।
কথাটা সত্যিও হতে পারে। এখানে আমার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে সবার ধারণা অনুযায়ী সোল ৬-এ নয়।
দেখা যাক কী হয়… কোত্থেকে শুরু করব?
এরিস প্রোগ্রাম। মঙ্গল তথা পৃথিবীর বাইরে কোন গ্রহে মানবজাতির প্রথম পদক্ষেপ… ইত্যাদি নানা হাবিজাবি কথা। এরিস ১-এর ক্রুরা নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সেরে নায়ক সেজে ফিরেছে পৃথিবীতে। প্যারেড, সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা… পেয়েছে সব।
মঙ্গলের আরেকটা জায়গায় অবতরণ করা এরিস ২-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাড়ি ফেরার পর উষ্ণ করমর্দনের পাশাপাশি ওটার ক্রুদের কপালে জুটেছে গরম কফি।
এরিস ৩… এটা আমার মিশন। আসলে আমার না ঠিক, মিশনের দায়িত্বে কমান্ডার লুইস ছিলেন। আমি কেবল তার একজন ক্রু। সত্যি বলতে, সবচেয়ে কম কর্মক্ষম ক্রু। যদি একজনের মিশন হত এটা, তবেই কেবল দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপার সম্ভাবনা ছিল।
কিন্তু এখন? আমিই তো নেতৃত্বে।
জানি না দলের বাকি সদস্যরা বুড়ো হয়ে মরার আগে এই লগ উদ্ধার হবে কি না। আশা করি সবাই ঠিকমতো পৃথিবীতে পৌঁছাবে। বন্ধুরা, যদি এই লেখা তোমরা পাও তাহলে জেনে রেখো- তোমাদের দোষ দিচ্ছি না। যা করণীয় ছিল, তাই করেছ সবাই। তোমাদের জায়গায় থাকলে হয়তো আমিও একই কাজ করতাম। কাউকে দোষারোপ করব না, উল্টো তোমরা বেঁচে ফেরায় আমি আনন্দিত।
মনে হচ্ছে, মঙ্গলে আসার মিশনগুলোর ব্যাপারে একটু বলে রাখা উচিত। স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছাই আমরা। হার্মিসে আসি যে কোন একটা সাধারণ শিপে চড়ে। মঙ্গলে আসা-যাওয়ার বেলায় সব এরিস মিশনই হার্মিসকে ব্যবহার করে আসলে। আকারে বেশ বড় এই স্পেসশিপ, বানাতে খরচাও লাগে বেশ। তাই একটার বেশি বানানোর ঝক্কিতে যায়নি নাসা।
হার্মিসে ঢোকার পর, বাড়তি চারটা রোবটিক মিশনে করে ফুয়েল আর রসদ আসে আমাদের জন্য। ততদিনে আমরা যাত্রার জন্য তৈরি করতে থাকি নিজেদের। সব ঠিকঠাক থাকলে শুরু হয় মঙ্গলযাত্রা।
ভারী কেমিক্যাল ফুয়েল পোড়ানো আর ট্রান্স-মার্স ইঞ্জেকশন অরবিটের দিন ফুরিয়েছে। হার্মিস চলে আয়ন ইঞ্জিনের মাধ্যমে। শীপের পেছনদিক থেকে তীব্র বেগে আর্গন পরিচালনা করা হয়, এতে ধীরগতিতে আগে বাড়ে হার্মিস। অন্যান্য বিক্রিয়কের মতো খুব একটা ভর নেই আর্গনের। তাই ধ্রুবগতিতে চলতে থাকি আমরা এভাবে। তবে পাওয়ারের জন্য নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর কিন্তু বাদ দেয়া হয়নি।
চাইলে বলতে পারি, মিশনে কতটা মজা হয় আমাদের মাঝে। তবে এখনই ব্যাপারটা ফাঁস করতে চাইছি না। শুধু জেনে রাখুন, যাত্রাপথের ১২৪টা দিন আমরা একে অন্যের গলা টিপে ধরে রাখিনি।
পৌঁছানোর পর এমডিভি (মার্স ডিসেন্ট ভেহিকল) নিয়ে সারফেসে নামি আমরা। জিনিসটাকে বড় কোন ক্যানের সাথে তুলনা করা যায়। সাথে যুক্ত থাকে কিছু লাইট থ্রাস্টার আর প্যারাশুট। এমডিভির একমাত্র উদ্দেশ্য, ছয়জন নভোচারীকে মঙ্গলের কক্ষপথ থেকে জীবিত অবস্থায় মাটির উপর নামিয়ে দেয়া।
এবার আসি অভিযানের আসল তেলেসমাতিতে। আগে থেকেই ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকে সব জিনিসপত্র।
সারফেসে অপারেশন চালানোর জন্য যা যা দরকার, মোট চোদ্দটা রোবটিক মিশনে করে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয় মঙ্গলে। আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়, যেন একই অবস্থানে নামে সবগুলো জিনিস। মানুষের মতো নাজুক না হওয়ায় অবশ্য সেগুলোর ঝাঁকিহীন অবতরণ প্রক্রিয়ার দিকে অতটা নজর রাখা হয় না।
সাধারণত, সবগুলো জিনিস নিরাপদে পৌঁছেছে- নিশ্চিত হওয়ার আগে আমাদের মিশনে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। সাপ্লাই মিশনসহ এসব হাবিজাবি মিলিয়ে তাই একেকটা অভিযানে সময় লাগে প্রায় তিন বছর। এরিস ২-এর মিশন ক্রুরা যখন বাড়ি ফিরছিল, ততদিনে শুরু হয়ে গেছে এরিস ৩-এর রসদসামগ্রী পাঠানো।
এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এমএভি বা ম্যাভ (মার্স এসেন্ট ভেহিকল)। সারফেস অপারেশন সেরে এটাতে করেই আবার হার্মিসে ফিরে আসব আমরা। তাই সবকিছুর মধ্যে এটা যেন বহাল তবিয়তে মঙ্গলে নামতে পারে, তা নিশ্চিত করা হয়। যোগাযোগ থাকে সরাসরি হিউস্টনের সাথে। যদি দেখা যায়, ম্যাভে কোন সমস্যা হয়েছে… তাহলে মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ ছাড়াই আবার ফিরতি পথ ধরার কথা আমাদের।
মঙ্গলের সারফেসে ম্যাভের কার্যপদ্ধতিও অদ্ভূত। এখানে আনা প্রতি কিলো হাইড্রোজেন দিয়ে ওটার তেরো কিলো ফুয়েল তৈরি করা যায়। প্রক্রিয়াটা বেশ মন্থর। ট্যাংক ভরতে সময় লেগে যায় প্রায় চব্বিশ মাস। এজন্য আমরা আসার অনেক আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয় ম্যাভ।
এবার ভাবুন, যখন দেখলাম- আমাকে ছাড়াই চলে গেছে জিনিসটা, কেমন হতে পারে অনুভূতি!
আমার প্রায় মরতে বসার ব্যাপারটা খুব আজব ছিল। বেঁচে থাকা তো আরও আজব।
একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগের বাতাস সহ্য করার মতো ক্ষমতা ছিল আমাদের মিশনের। তাই যখন হিউস্টন থেকে দেখল, বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় একশো পঁচাত্তর ছাড়িয়েছে… তখন কিংকর্তব্যবিমুঢ় হওয়াই স্বাভাবিক। স্পেসসুট পরে হ্যাবের ভেতর বসে ছিলাম আমরা, যাতে প্রেশার লস না হয়। কিন্তু সমস্যাটা হ্যাব নিয়ে না।
ম্যাভ আদতে একটা স্পেসশিপ। নাজুক অংশের অভাব নেই ওটার। নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে ঝড়ের মোকাবেলা করতে থাকলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে যে কোন সময়। তাই দেড় ঘণ্টা বাতাসের প্রবল ঝাপ্টা সওয়ার পর, নাসা থেকে মিশন অ্যাবোর্ট করার নির্দেশ এলো। আমরা কেউ চাইনি, মাসখানেক লম্বা মিশন মাত্র ছয় দিনে ডিসমিস হোক। কিন্তু ম্যাভের কিছু হলে আটকা পড়ে যেতে হবে এখানে।
তাই হ্যাব থেকে বেরিয়ে ম্যাভে চড়ার জন্য রওনা হলাম। কাজটা ঝুঁকির। কিন্তু মানতে হবে, ডর কি আগে জিত হ্যায়।
সবাই সহি-সালামতেই পৌঁছে যায় গন্তব্যে, স্রেফ আমি ছাড়া।
আমাদের প্রধান স্যাটেলাইট ডিশ, যা যোগাযোগ রাখে হ্যাব থেকে হার্মিসে, বাতাসের তোড়ে একটা প্যারাশুটের মতো উড়ে এসে বাড়ি খায় রিসিপশন অ্যান্টেনায়। তারপর ভাঙা অ্যান্টেনা ছুটে এসে বুলেটের মতো গেঁথে ফেলে আমাকে।
ভাই রে ভাই, জীবনে এত ব্যথা কখনও পাইনি! মনে আছে, বাতাসের ঝাপ্টায় উল্টে পড়ে যাই সাথে সাথে। সুট থেকে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় কানে বাজছিল ক্রমাগত শোঁশোঁ আওয়াজ।
জ্ঞান হারানোর আগে সর্বশেষ দেখা দৃশ্য হলো, সহকর্মী জোহানসেন হতাশ ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।
জেগে উঠলাম সুটের অক্সিজেন অ্যালার্ম শুনে। ঝড় থেমে গেছে। মুখ থুবড়ে পড়ে আছি আমি। বালুতে প্রায় ঢাকা পড়া গোটা শরীর। সবার আগে মনে হলো এই কথাটা- শালা মরিনি কেন!
স্যুট আর আমার শরীর ভেদ করে যাওয়ার মতো যথেষ্ট গতি অ্যান্টেনার ছিল। কিন্তু পেলভিসের হাড়ে লেগে থেমে যেতে হয় বেচারাকে। ফলে একটামাত্র ছিদ্র হয়েই সন্তুষ্ট থাকে আমার স্যুট… বলা বাহুল্য, সেই সাথে শরীরটাও।
কিছুদূর গড়িয়ে এসে একটা পাহাড়ের গোড়ায় থামি আমি। উপুড় হয়ে থাকায় চাপ পড়ে অ্যান্টেনার উপর। ফলে দুর্বল একটা সিল তৈরি হয়ে স্যুটে। তারপর ক্ষত থেকে বেরোনো রক্ত এসে জমা হয় ফুটোর গোড়ায়। বাতাসের গতি আর চাপের কারণে প্রায় সাথে সাথে শুকিয়ে যায় জলীয় অংশ। ক্রমে আরও রক্ত এসে জমা হয় শুকনো অংশের পেছনে। এতে আরেকটু পোক্ত হয় গাঁথুনি।
স্যুটটা অবশ্য ওদিকে নিজের কাজ বন্ধ রাখেনি। বাতাসের চাপের তারতম্য লক্ষ্য করে ওটা আমার নাইট্রোজেন ট্যাংক থেকে ক্রমাগত শ্যূন্যস্থান পূরণ করছিল। তবে কিছুক্ষণ পর স্যুটের কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্বারের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। সুরক্ষার জন্য ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাথে করে শুধু অক্সিজেন বহন করলেই হয় না, পাশাপাশি বের করে দিতে হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডও। হ্যাবে আমাদের কাছে অক্সিজেনাটর থাকে। বিশাল এই যন্ত্রের কাজ হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ভেঙে অক্সিজেন ফিরিয়ে আনা। কিন্তু হালকা-পাতলা হওয়ার দরুণ স্পেসস্যুটে এই জিনিস নেই। তাই সাধারণ ফিল্টারের মাধ্যমে শোষন প্রক্রিয়া চলমান রাখা হয়। যতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, ততক্ষণে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আমার ফিল্টারগুলোর।
এই সমস্যা সনাক্ত করার পর প্রতিকার হিসেবে বিশেষ এক অবস্থায় চলে যায় স্যুটটা, ইঞ্জিনিয়াররা একে বলে- ব্লাডলেটিং। কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে কারিকুরি ফলানোর কোন উপায় না পেয়ে ওটা ক্রমাগত পরিবেশে দূষিত বাতাস বের করে দিতে থাকে। এবং শূণ্যস্থান পূরণ করতে থাকে নাইট্রোজেনের মাধ্যমে। সেই ট্যাঙ্ক খালি হলে ডাক পড়ে অক্সিজেনের।
আমাকে জীবিত রাখার জন্য এই কাজটাই করেছে স্পেসস্যুট। বাতাসের অভাব পূরণ করেছে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দিয়ে। এতেও শান্তি নেই। অক্সিজেনের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে গ্যাসটা আমার স্নায়ুতন্ত্র, ফুসফুস, চোখ ইত্যাদি বিকল করে দেবে। কী আজব কারবার দেখুন- প্রথমে ফুটোর কারণে অক্সিজেন স্বল্পতার ঝুঁকি… এরপর আবার আধিক্য!
তো এই যে এতগুলো প্রক্রিয়ার কথা বললাম, প্রতিটারই আলাদা আলাদা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরল ওই অক্সিজেন অ্যালার্মে।
স্পেস মিশনের ট্রেনিং কোন হেলাফেলার বিষয় না। পৃথিবীতে প্রায় এক সপ্তাহ স্যুট নিয়ে ড্রিল করে কাটিয়েছি। জানি কি করতে হবে।
হেলমেটের পাশ থেকে সাবধানে ব্রিচ কিট খুলে নিলাম। জিনিসটা দেখতে ফানেলের মতো। এক মাথায় ছোট্ট ভাল্ভ, অন্যদিকে প্রশস্থ অংশে আঠালো রেজিন। করণীয় কাজ হলো- আপনাকে প্রথমে ভাল্ভ খোলা রেখে মোটা অংশটা জুড়ে দিতে হবে ফুটোর উপর। বাতাস ভাল্ভের মাধ্যমে বের হতে পারবে, তাই রেজিনের দিকটা স্যুটে লেগে থাকায় সমস্যা হবে না। তারপর ভাল্ভ বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান।
আসল ঝামেলা ছিল অ্যান্টেনাটা ক্ষত থেকে সরানো। জিনিসটা আঁকড়ে ধরে টান দিলাম যত জোরে সম্ভব। হুশ করে বাতাস বেরোনোর পাশাপাশি আগুন জ্বলে উঠল যেন ক্ষতস্থানে। দেরি না করে ব্রিচ কিট দিয়ে বন্ধ করে দিলাম ফুটো। শূন্যস্থান পূরণ হয়ে গেল অক্সিজেন দিয়ে। হাতের স্ক্রিনে রিডআউট দেখলাম- অক্সিজেনের মাত্রা এখন ৮৫%। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ২১% থাকে সাধারণত। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হলেও বেঁচে যাব, কারণ এই অবস্থায় চিরকাল থাকতে হবে না আমাকে।
পাহাড় পেরিয়ে হ্যাবের দিকে এগোনোতে মন দিলাম। চূড়ায় উঠে একইসাথে ভালো আর খারাপ- দুই ধরণের অনুভূতি হলো। ভালো কারণ হ্যাবটা এখনও অক্ষত, খারাপ কারণ ম্যাভ সামনে থেকে উধাও।
বাঁশ খাওয়ার ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই। তবে এটাও জানি, এখানে এভাবে মরা চলবে না। তাই পায়ে পায়ে হ্যাবে ফিরে আটকে দিলাম এয়ারলক। বাতাসের চাপ স্বাভাবিক হওয়ার পর ছুঁড়ে ফেললাম মাথার হেলমেট।
স্যুট খুলে সবার আগে মন দিলাম ক্ষতস্থানে। সেলাই লাগবে। কপাল ভালো, আমাদের সবার সাধারণ মেডিক্যাল ট্রেনিং আছে। সেই সাথে হ্যাবেও মজুদ আছে বেশ ভালো পরিমাণ মেডিক্যাল সাপ্লাই। লোকাল অ্যানেস্থেটিকের এক শট, ক্ষতস্থান পরিষ্কারের পর মোটমাট নয়টা সেলাই। কাজ শেষ। কয়েক সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিকের উপর থাকতে হবে, তবে মরব না।
জানি কাজ হবে না, তাও কমিউনিকেশন অ্যারেতে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। বলা বাহুল্য, নো সিগন্যাল। প্রাইমারি স্যাটেলাইট ডিশ ভাঙা। সাথে করে নিয়ে গেছে রিসিপশন অ্যন্টেনা। হ্যাবে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি কমিউনিকেশন সিস্টেম আছে, কিন্তু ওগুলো দিয়ে শুধু ম্যাভের সাথে যোগাযোগ করা যায়। সেখান থেকে আরও শক্তিশালী সিস্টেম হয়ে সিগন্যাল পৌঁছায় হার্মিসে। তবে তার জন্য ম্যাভ কাছেপিঠে থাকা চাই।
ভাঙা যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করার একটা চেষ্টা চালানো যায়, তবে সময় লেগে যাবে কয়েক সপ্তাহ। ওদিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মঙ্গলের কক্ষপথ ছেড়ে যাবে হার্মিস। যত দ্রুত রওনা হবে, অরবিটাল ডায়নামিক্সের কারণে তত নিরাপদ হবে যাত্রাপথ। অতএব ওদের অপেক্ষা করার প্রশ্নই আসে না।
স্যুট পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার বায়ো-মনিটর কম্পিউটারের দফারফা করে দিয়েছে অ্যান্টেনাটা। মিশন চলাকালীন বাইরে থাকার সময়টুকুকে আমরা বলি ইভিএ বা এভা। তো এই এভা করার সময় সব ক্রু-দের স্যুটগুলো একটা নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকে, যাতে একে অন্যের শারীরিক গতিবিধির উপর নজর রাখতে পারে। ঝড়ের সময় হয়তো সবাই দেখেছে- আমার স্যুটের এয়ার প্রেশার শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় বায়ো-সাইনেরও হদিস নেই। একইসাথে গড়িয়ে পড়েছি কয়েক হাত দূরে পাহাড়ের নিচে, পেটে গাঁথা বল্লম। আমাকে যে সবাই মৃত ভাববে, তাতে আর আশ্চর্যের কী!
সম্ভবত লাশ উদ্ধার নিয়ে আলোচনা করেছে ওরা। কিন্তু নিয়মকানুন পরিষ্কার- মিশন চলাকালে মঙ্গলে যদি কেউ মারা যায়, তাকে ওখানেই ফেলে আসতে হবে। কারণ এতে ম্যাভে বাড়তি ওজন বইতে হবে না। ফুয়েল আর থ্রাস্টে চাপ পড়বে কম। জীবিতদের নিয়ে ঝুঁকির সামনে মৃতদের নিয়ে আবেগের দাম নেই।
তো এই হচ্ছে সার্বিক পরিস্থিতি। ফেঁসে আছি মঙ্গলে। হার্মিস বা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের উপায় নেই। সবাই ভাবছে আমি মৃত। এখন আছি এমন এক হ্যাবে, যেটা একত্রিশ দিন টেকার মতো করে বানানো।
অক্সিজেনাটর বিকল হয়ে গেলে, দম আটকে মরব। পানির ফিল্টার নষ্ট হলে, মারা যাব পিপাসায়। হ্যাব ফুটো হলে, বিস্ফোরিত হব বোমার মতো। যদি এসবের কিছু না হয়… তবুও মরব না খেতে পেয়ে।
আছোলা বাঁশ আর কাকে বলে!
-Andy Wier
Translated by Adnan Ahmed Rizon
Published by Rodela Prokashoni