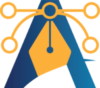অধ্যায় এক
রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে ম্যালরি, ভাবছে।
হাত ভেজা। কাঁপছে ও। চিন্তিত ভঙ্গীতে পায়ের আঙুল ঠুকছে ভাঙা টাইলসের মেঝেতে। ভোর হবে হবে ভাব। সূর্য মনে হয় সবেমাত্র উঁকি দিচ্ছে দিগন্তে। আবছা আলোর পরত লাগায় জানালার ভারী পর্দায় ঘাপটি মেরে থাকা অন্ধকার ফিকে হয়েছে একটু। দেখতে দেখতে নতুন চিন্তা উদয় হলো ম্যালরির মনে।
কুয়াশা…
কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে হলের নিচে ঘুমায় বাচ্চারা। হয়তো একটু আগে উঠান থেকে আসা আওয়াজ শুনেছে। ম্যালরির সৃষ্টি করা শব্দ মাইক্রোফোন পেরিয়ে বিছানার পাশের অ্যামপ্লিফায়ার পর্যন্ত না আসার কোন কারণ নেই।
নিজের হাতের দিকে তাকাল ও। মোমের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হাতগুলো ভেজা। সকালের শিশির এখনও লেগে আছে তালুতে।
মোমবাতি নেভানোর আগে বড় করে নিঃশ্বাস নিল ম্যালরি। তারপর চোখ বুলাল ছোট্ট ঘরের চারপাশে। জিনিপত্রে মরিচা ধরেছে। বাসনকোসনগুলো ভাঙা। কার্ডবোর্ডের বক্স ব্যবহৃত হয়েছে ময়লার ঝুড়ি হিসেবে। চেয়ারগুলোর কয়েকটা সুতো দিয়ে বাঁধা। নোংরা দেয়ালে বাচ্চাদের হাত-পায়ের ছাপ। কিছু পুরনো দাগও রয়েছে।
হলের দেয়ালের নিচের অংশে রঙ চটে গেছে। এককালের বেগুনি আজ পরিণত হয়েছে বাদামিতে। এগুলো রক্ত। লিভিং রুমের কার্পেটও বিবর্ণ। ম্যালরি প্রাণপণে ঘষেও দাগ তুলতে পারেনি। কাজে লাগানোর মতো কোন কেমিক্যাল নেই বাড়িতে। অনেক আগে বালতিতে করে কুয়া থেকে পানি এনেছিল ও, তারপর স্যুট কোট ভিজিয়ে ঘষে ঘষে চেষ্টা করেছে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানোর।
নাছোড়বান্দা দাগগুলো হার মানেনি। এমনকি যা-ও কিছুটা গেছে, ছায়ার মতো নিজেদের ছাপ রেখে যেতে ভোলেনি। ফয়ারের একটা ফোকরে এক বক্স মোমবাতি রাখা ছিল। লিভিং রুমের কাউচ অদ্ভূতভাবে বাঁকানো। ল্যাপ্টানো দুটো দাগের উপর চাপা দেয়া, যা দেখে ম্যালরির নেকড়ের মাথা বলে মনে হয়।
দ্বিতীয় তলায় সিঁড়ির উপরে একগাদা ছাতাপড়া পুরনো কোট, বেগুনি দাগে ভর্তি, দেয়ালের ভেতর গেঁথে আছে যেন। তার দশ ফুট সামনে গোটা বাড়ির সবচেয়ে বিচ্ছিরি কালচে দাগটা। দ্বিতীয় তলার অপর প্রান্তে কী আছে, ম্যালরি জানে না। কারণ ওই দাগ অতিক্রম করার সাহস তার হয়নি।
একসময় ডেট্রয়েট শহরতলীর খুব সুন্দর একটা বাড়ি ছিল এটা। নিরাপদ, অভিজাত… একটা পরিবারের থাকার পক্ষে উপযুক্ত। মাত্র পাঁচ বছর আগে হয়তো কোন রিয়েল-এস্টেট এজেন্ট গর্বভরে এই বাড়ির গুণকীর্তন করত কাস্টোমারদের সামনে।
কিন্তু আজ পরিস্থিতি সম্পুর্ণ আলাদা। জানালাগুলোতে কার্ডবোর্ড আর কাঠের আস্তর দেয়া। পানির লাইন অচল। কিচেন কাউন্টারের উপর বিশাল একটা কাঠের বালতি। স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। বাচ্চাদের খেলার মতো কোন খেলনা নেই, তাই একটা চেয়ারের ভাঙা টুকরো ওদের সম্বল। কাঠের টুকরোগুলোর উপর কাঁচা হাতে আঁকা ছোট ছোট মুখ। কাপবোর্ডগুলো খালি। দেয়ালে কোন ছবি আঁকা নেই এখানে।
পেছনের দরজার নিচ থেকে তার বেরিয়ে এসে ঢুকেছে একতলার বেডরুমে, যার সাথে যুক্ত অ্যামপ্লিফায়ারগুলো বাইরে থেকে কোন আওয়াজ এলে ম্যালরি আর বাচ্চাদের সতর্ক করে। এভাবেই কাটছে তিনজনের জীবন। অনেক দিন হয় কেউ বাইরে যায়নি। আগে যখন গিয়েছে, চোখে বাঁধা ছিল পট্টি।
বাড়ির বাইরের দুনিয়া কেমন হতে পারে, সেসম্পর্কে বাচ্চাদের কোন ধারনা নেই। এমনকি জানালা দিয়েও তাকানোর অনুমতি নেই ওদের। ম্যালরি নিজেও চার বছর ধরে চোখ রাখে না জানালার ফ্রেমের ওপাশে।
চারটা বছর…
আজ এই সিদ্ধান্তটা না নিলেও চলে। মিশিগানে এখন অক্টোবর মাস চলছে। বেশ ঠাণ্ডা। নদী ধরে বিশ মাইল পথ বাচ্চা দুটোর পক্ষে সহজ হবে না। খুব কম বয়স ওদের। যদি কেউ একজন পানিতে পড়ে যায়? চোখ বাঁধা অবস্থায় ম্যালরি কী করবে তখন?
একটা দুর্ঘটনা, ম্যালরি মনে মনে ভাবল। খুব বাজে ব্যাপার হবে। এতদিন ধরে এত এত কষ্ট, বেঁচে থাকার এত মরিয়া প্রচেষ্টার পর মরতে হবে একটা সাধারণ দুর্ঘটনায় পড়ে।
পর্দাগুলোর দিকে তাকাল ম্যালরি। কাঁদতে শুরু করল আবার। কারও উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে মন চাইছে। কারও কাছে মিনতি করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু কথা শোনার মতো কেউ নেই। এসব ঠিক না, বলতে চাইল ও। নিষ্ঠুর পরিস্থিতি।
কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে তাকাল ম্যালরি। কিচেনে ঢোকার মুখ, বাচ্চাদের বেডরুমে যাওয়ার হল। পাল্লাহীন দরজার ফ্রেমের ওপাশে নীরবে ঘুমাচ্ছে বাচ্চারা। কালো কাপড়ে মোড়া ছোট্ট শরীর দুটো, আলো ঢোকার সুযোগ নেই। নড়ছে না কেউ। বোঝা যাচ্ছে, জেগে ওঠেনি। তবু হয়তো শুনতে পাচ্ছে ওরা। এই একটা কাজই ভালো পারে বাচ্চা দুটো। জন্মের পর থেকে ম্যালরি ওদের শুধু কানের উপর ভরসা করতে শিখিয়েছে। তাই এখন মাঝে-মাঝে ওর মনে হয়, বাচ্চারা হয়তো ওর চিন্তার ফিসফিসানিও টের পায়।
সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে ম্যালরি। আকাশে উজ্জ্বল আলো থাকবে তখন। নৌকায় আরও বেশি নজর দেয়া যাবে। বাচ্চাদের বলে দিতে হবে চারদিকে কান পেতে রাখার জন্য। মাত্র চার বছর বয়স ওদের, তবে শব্দ শোনার ক্ষেত্রে পটু হয়ে ওঠেছে দু’জনেই। চোখ বাঁধা অবস্থায় একা নৌকা চালানো পাগলের প্রলাপের মতো শোনায়। বাচ্চাদের সাহায্য চাই ম্যালরির। ওদের কানের উপর ভরসা করতে হবে। কিন্তু মাত্র চার বছর বয়সে পরামর্শ দেয়ার মতো যোগ্যতা বাচ্চাদের হয়েছে তো? বাড়ি ছাড়ার জন্য তৈরি তো ওরা? চিরকালের জন্য?
কিচেনের একটা চেয়ারে বসে কান্না আটকানোর চেষ্টা করল ম্যালরি। জুতা খোলা পায়ের আঙুল এখনও আনমনে মেঝেতে ঠুকছে। আস্তে আস্তে সেলারের সিঁড়ির দিকে তাকাল এরপর। ওখানে দাঁড়িয়ে একসময় টম নামে একজনের সাথে কথা বলেছে ও… ডন নামে আরেকজনের ব্যাপারে। তারপর চোখ ফেরাল সিংকের উপর। ওখানে একসময় কুয়া থেকে বালতি বালতি পানি তুলে আনত ডন। ভয়ে কাঁপত বাইরে থেকে ফেরার পর। সামনে ঝুঁকে ফয়ার দেখতে পেল ম্যালরি। শেরিল ওখানে দাঁড়িয়ে পাখিদের জন্য খাবার তৈরি করত। সামনের দরজার আগে হচ্ছে লিভিং রুম। এখন অন্ধকার আর নীরব হলেও জায়গাটা এককালে অনেকগুলো লোকে গিজগজ করত। মনে পড়লে ম্যালরি স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠে।
মাত্র চারটা বছর, মনে মনে বলল ও। সাথে সাথে ইচ্ছা হলো সর্বশক্তিতে ঘুসি হাঁকায় দেয়ালে।
ম্যালরি জানে, এই চার বছর খুব সহজে আট বছরে রূপ নিতে পারে। তারপর বারো। ততদিনে বড় হয়ে যাবে বাচ্চারা। তবু আকাশ দেখা জুটবে না কারও ভাগ্যে। কখনও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবে না ওরা। এভাবে মনে মনে এই অতিরিক্ত বারোটা বছর বেঁচে থাকার মানে কী? চোখে বাঁধা পট্টির আড়াল এভাবে বাঁচাকে কি আদৌ জীবনে বলা যায়?
ঢোক গিলল ম্যালরি। ভাবছে সম্ভাবনাটার কথা। সে কি পারবে বড় হওয়া অব্দি এভাবে ওদের দেখভাল চালিয়ে যেতে?
কতদিন ধরে চলবে এসব? আগামী দশ বছর? যতদিন না বাচ্চারা বড় হয়ে মায়ের দেখভালের দায়িত্ব নেয়? এমন করে লাভটাই বা কী?
তুমি খুব খারাপ মা, নিজেই নিজেকে বলল তারপর।
আকাশের বিশালতা বোঝে না বাচ্চারা। খোলা মাঠে দৌড়াতে পারে না। রাস্তাঘাট, অলিগলি, পাশের বাড়ির প্রতিবেশী সম্পর্কে কোন ধারনা ওদের নেই। জানে না রাতের আকাশে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা তারা দেখার আনন্দ কেমন হতে পারে।
এমন এক জীবন সে ওদের উপহার দিচ্ছ, যেটাকে আসলে জীবন বলা চলে না।
পানিতে ঝাপসা হয়ে থাকা দৃষ্টিতে দেখল ম্যালরি, পর্দার ওপাশে অন্ধকার আরেক পোঁচ সাদা হয়েছে। বাইরের কুয়াশা বেশিক্ষণ থাকবে না। হয়তো এই ঘোলাটে পরিবেশই গা বাঁচিয়ে নদী পর্যন্ত যেতে সবাইকে সাহায্য করবে। এখনই জাগিয়ে দিতে হবে বাচ্চাদের।
কিচেনের টেবিলে দুম করে থাবা বসাল ম্যালরি। মুছল দুই চোখ। তারপর উঠে হল ধরে গিয়ে ঢুকল বাচ্চাদের বেডরুমে।
‘ছেলে!’ চেঁচিয়ে ডাকল ও। ‘মেয়ে! উঠে পড়ো সবাই!’
ঘরটা অন্ধকার হয়ে আছে। একটামাত্র জানালা, তাও মোটা কম্বল দিয়ে ঢাকা। সূর্যের আলোর এখানে আসার অধিকার নেই। ঘরের দুই পাশে দুটো ম্যাট্রেস। উপরে কালো ডোম। আকৃতিগুলোকে খাড়া করে রাখা তারগুলো একসময় বাড়ির পেছনে ছিল, কুয়ার পাশে ছোট বাগানে বেড়া হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু বিগত চার বছর ধরে কাজে লাগছে ছাউনি হিসেবে। ভেতরে ঘুমানো বাচ্চাদের দৃষ্টি সামলে রাখে।
ডোমগুলোর ভেতর নড়াচড়া টের পেল ম্যালরি। তারপর উবু হয়ে বসে মেঝেতে পোঁতা পেরেক থেকে খুলে দিল তারের প্রান্ত। অন্য হাতে পকেট থেকে বের করে আনছে পট্টি। বাচ্চা দুটোর ঘুম ঘূম চোখে পরিয়ে দেবে।
‘মা?’
‘উঠে পড়ো জলদি। মা চায় তোমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হও।’
সাথে সাথে সাড়া দিল দু’জন। কোন মোচড়ামুচড়ি নেই, অভিযোগ নেই।
‘কোথায় যাব আমরা?’ মেয়েটা জানতে চাইল।
ওর হাতে একটা পট্টি ধরিয়ে দিল ম্যালরি। ‘এটা পরে নাও। আমরা নদীর দিকে যাব।’
চটপট কালো কাপড় দুটো চোখে দিল বাচ্চারা। অভ্যস্ত হাতে মাথার পেছনে বেঁধে ফেলল দুই প্রান্ত। এই কাজটা ওদের খুব পরিচিত। সব স্বাভাবিক থাকলে হয়তো চার বছর বয়সে কোন খেলাধুলার সাথে এভাবে পরিচিত হতো দু’জন, ভাবতে ম্যালরির বুক ফাঁকা হয়ে গেল। সাধারণত এই বয়সে বাচ্চাদের মনে প্রচণ্ড কৌতূহল কাজ করে। ওদের জিজ্ঞেস করা উচিত- কেন নদীর দিকে যেতে হবে? কিংবা আজকেই কেন? কিন্তু এসব না করে ওরা স্রেফ মায়ের আদেশ পালন করছে।
ম্যালরি এখনও নিজের পট্টি চোখে বাঁধেনি। আগে বাচ্চাদের তৈরি করতে হবে।
‘তোমার পাযল সাথে নাও,’ মেয়েকে বলল ও। ‘আর হ্যাঁ, দু’জনেই নিজ নিজ কম্বল নেবে।’
মনে মনে খুব উত্তেজনা বোধ করছে ম্যালরি। ব্যাপারটা হিস্টিরিয়ার চেয়ে খারাপ। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে গিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল ও। দরকারি জিনিস খুঁজছে, যা হয়তো পথে কাজে লাগতে পারে।
হঠাৎ নিজেকে খুব অপ্রস্তুত মনে হলো ম্যালরির। নিরাপত্তার খুব অভাব বোধ হচ্ছে। পায়ের নিচের মেঝে যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে, বাড়িটাও তাই। অনিশ্চিত পৃথিবীতে ও এখন একা। নিজের অজান্তেই পট্টিটা মুঠো করে ধরল ম্যালরি। জানে যত জিনিসপত্র সাথে নিক না কেন, অস্ত্র হিসেবে যা-ই ব্যবহার করুক, এই পট্টির চেয়ে বড় নিরাপত্তা অন্য কিছু দিতে পারবে না।
‘কম্বল নিয়ে এসো!’ বাচ্চাদের মনে করিয়ে দিল ম্যালরি। শুনতে পাচ্ছে দুটো ছোট্ট শরীরের হুটোপুটির আওয়াজ। অপেক্ষা না করে তারপর নিজেই এগোল ওদের সাহায্য করার জন্য।
ছেলেটার শারীরিক গঠন বয়সের তুলনায় একটু কম; তবে শক্তপোক্ত গড়ন, এজন্য ম্যালরি বেশ গর্ব অনুভব করে। দুটো শার্টের দিকে দ্বিধান্বিত চোখে তাকাচ্ছে এখন। ভাবছে কোনটা পরবে। তবে দুটো কাপড়ই ওর তুলনায় বড়। এগুলোর আসল মালিক ছিল…
থাক সে কথা।
ছেলের জন্য একটা কাপড় পছন্দ করে দিল ম্যালরি। সাথে সাথে ছেলেটার কালো চুল হারিয়ে গেল শার্টের নিচে, বের হলো মাথার ফুটো দিয়ে। মাপ দেখে ম্যালরি বুঝতে পারল, ও সম্প্রতি গায়েগতরে একটু বেড়েছে।
মেয়েটার শারীরিক গড়ন অবশ্য বয়সের তুলনায় ঠিকঠাক। মাথা আগে দিয়ে একটা জামার ভেতর ঢুকতে চাইছে ও। পুরনো বিছানার চাদর দিয়ে বানানো কাপড়টা ম্যালরির সেলাই করা, বাচ্চাটা নিজেও সাহায্য করেছিল।
‘বাইরে খুব ঠাণ্ডা, মেয়ে। এক জামায় কাজ হবে না।’
বাচ্চাটা ভ্রুকুটি করল। সদ্য ঘুম ভাঙায় এলোমেলো হয়ে আছে সোনালি চুল।
‘আমি প্যান্টও পরব, আম্মু। আর কম্বল তো সাথে নেবই।’
ম্যালরির রাগ হলো। নিজের কথায় কোন প্রতিবাদ শুনতে চায় না ও। অন্তত আজকের দিনে নয়। এমনকি বাচ্চাদের কথায় যুক্তি থাকা সত্ত্বেও না।
বাইরের দুনিয়ার পরিত্যক্ত মল-রেস্টুরেন্ট, হাজার হাজার নষ্ট গাড়ি, দোকানের তাকে পচে যাওয়া জিনিসপত্র ইত্যাদি সব যেন তাকিয়ে আছে এই বাড়ির দিকে। ফিসফিস করে সতর্ক করছে অনাগত বিপদের ব্যাপারে।
বেডরুমের ক্লযেট থেকে একটা কোট তুলে নিল ম্যালরি। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এই শেষ। আর কখনও ফিরবে না এখানে।
‘আম্মু,’ হল থেকে মেয়েটা ডাকল। ‘আমাদের বাইসাইকেল হর্নগুলো দরকার হবে নাকি?’
ম্যালরি নাক দিয়ে বড় করে বাতাস টানল।
‘না,’ জবাব দিল তারপর। ‘আমরা সবাই একসাথে থাকব। সবসময়।’
মেয়েটা বেডরুমে ফিরে যেতে আবার চিন্তায় আচ্ছন্ন হলো ম্যালরির মন। কী হতাশাজনক ব্যাপার! বাইসাইকেল থেকে খুলে আনা এই হর্নগুলো বাচ্চাদের দেখা সবচেয়ে মজার জিনিস। বছরের পর বছর ধরে এগুলো দিয়ে খেলে আসছে ওরা। মাঝে-মাঝে লিভিংরুম থেকে ভেসে আসা টুংটাং আওয়াজে ম্যালরির মনে ভয় ধরে যেত। তবু বাধা দেয়নি ওদের খেলায়। কখনও লুকিয়েও রাখেনি জিনিসগুলো। নতুন মাতৃত্বের উদ্বিগ্ন মনেও ম্যালরি বুঝতে, বাচ্চাদের হাসির খোরাক হওয়া হর্নগুলো ওদের জন্য কতটা দরকারি।
মাঝে-মাঝে তো বেল বাজিয়ে ভিক্টরকে ভয় দেখাত ওরা।
আহ, ভিক্টর! কুকুরটাকে খুব ভালোবাসতো ম্যালরি। বাচ্চাদের বড় করে তোলার প্রথমদিকে যখন নদী ধরে পালানোর কথা ভাবত ও, সেই পরিকল্পনায় ভিক্টরকেও শামিল করে নিত। পাশে বসে হয়তো তাকে সতর্ক করতে পারতো কুকুরটা, কিংবা নিজেও মোকাবেলা করতে পারতো বাইরের কোন জীবজন্তু বা মানুষ হামলা চালালে।
‘ঠিক আছে।’ বাচ্চাদের বেডরুমের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল ম্যালরি। ‘হয়েছে। এবার চলো।’
আগে মাঝেমধ্যে বাচ্চাদের বলেছে ও, একদিন হয়তো এমন দিন আসবে। তবে নদী ধরে এগোনোর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছে নিছক একটা ভ্রমণ হিসেবে। ঘূণাক্ষরেও পালানোর নাম নেয়নি। এতে বাচ্চারা বুঝে ফেলত এতদিন ওরা যেভাবে বাঁচছে, তা থেকে একদিন পালিয়ে যেতে হবে।
এসবের বদলে ম্যালরি ওদের লোভ দেখিয়েছে ভবিষ্যতের… যেদিন তড়িঘড়ি করে জাগিয়ে দেবে ঘুম থেকে, চিরতরে চলে যেতে হবে এই বাড়ি ছেড়ে। চারটা বছর ধরে এই দিনের অপেক্ষায় ছিল ওরা। কাপবোর্ডে সবসময় ছোট্ট পাউচে খাবার মজুদ থাকত। পচে গেলে পাল্টে দেয়া হতো প্যাকেট। ম্যালরির বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ ছিল ওগুলো। দেখলে তো, কাপবোর্ডের এই খাবারগুলো আমাদের ওই পরিকল্পনার অংশ।
আজই সেই দিন। আজকের এই সকাল, এই মুহূর্ত, এই কুয়াশার চাদর।
বাচ্চা দুটো এগিয়ে এলে ম্যালরি ওদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। পরীক্ষা করে দেখল প্রত্যেকের চোখের পট্টি। সব ঠিকঠাক আছে। ছোট্ট মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ম্যালরি বুঝল, অবশেষে বাড়ি যাওয়ার জন্য ওরা তৈরি।
‘আমার কথা শোনো,’ কড়া গলায় বলল তারপর। ‘আজ একটা নৌকা নিয়ে নদী ধরে রওনা দেব আমরা। লম্বা রাস্তা হতে পারে। আমি যা বলব অক্ষরে অক্ষরে মানবে তোমরা, বুঝেছ?’
কচি গলায় আলাদা আলাদা জবাব এল।
‘হ্যাঁ।’
‘হ্যাঁ।’
‘বাইরে অনেক ঠাণ্ডা। প্রত্যেকের সাথে কম্বল আছে। চোখে বাঁধা থাকবে পট্টি। এর বেশি কিছু লাগবে না। বুঝতে পারছো আমার কথা?’
জবাব এল সাথে সাথে।
‘হ্যাঁ।’
‘হ্যাঁ।’
‘যা-ই হোক না কেন, কেউ চোখের বাঁধন খুলবে না। খুললে মার খাবে আমার হাতে। বুঝতে পেরেছ?’
‘হ্যাঁ।’
‘হ্যাঁ।’
‘তোমাদের সাহায্য লাগবে আমার। সতর্কভাবে কান পেতে রাখবে চারদিকে। নদীতে থাকার সময় পানির পাশাপাশি জঙ্গলের আওয়াজও শুনতে হবে। জীবজন্তুর শব্দ পেলে আমাকে জানাবে। পানিতে কিছু শুনলেও ডাকবে আমাকে। বুঝলে?’
‘হ্যাঁ।’
‘হ্যাঁ।’
‘অহেতুক কোন প্রশ্ন করবে না। ছেলে, তুমি বসবে নৌকার সামনের অংশে। মেয়ে, তুমি পেছনে। নৌকায় উঠে আমি যার যার জায়গায় বসিয়ে দেব তোমাদের। আর আমি থাকব মাঝে, দাঁড় বাওয়ার জন্য। বাড়তি কোন কথা বলা যাবে না। ঠিক আছে?’
‘হ্যাঁ।’
‘হ্যাঁ।’
‘গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে কোন কিছুর জন্য থামব না আমরা। পৌঁছে গেলে আমি বলব তোমাদের। তার আগে কোন ঝামেলা চাই না। খিদে পেলে এই পাউচ থেকে খাবে চুপচাপ।’
ছোট্ট হাতে খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দিল ম্যালরি।
‘ঘুমানো চলবে না। আবারও বলছি, ঘুমানো নিষেধ। তোমাদের কানের সাহায্য চাই আজ আমার। এজন্যই এভাবে তৈরি করেছি এতদিন।’
‘মাইক্রোফোন সাথে নেব আমরা?’ মেয়েটা জানতে চাইল।
‘না।’
বাচ্চাদের মুখের দিকে পালাক্রমে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করল ম্যালরি।
‘বাড়ি থেকে বের হয়ে হাতে হাত ধরে আমরা কুয়ার পাশের পথ ধরে এগোব। নদীর দিকে যে রাস্তাটা গেছে, ওখানে ঝোপঝাড় জন্মেছে। পরিষ্কার করার জন্য মাঝে-মাঝে হাত ছাড়া লাগতে পারে। তখন নিজেরা হাত ধরাধরি করে থাকবে তোমরা, একজন আঁকড়ে ধরে রাখবে আমার কোট। ঠিক আছে?’
‘হ্যাঁ।’
‘হ্যাঁ।’
বাচ্চাগুলোর গলায় ভয় খেলা করছে নাকি?
‘আমার কথা শোনো। আমরা এমন এক জায়গায় যাব যেখানে তোমরা আগে কখনও যাওনি। এই বাড়ি ছেড়েই কোনদিন বের হওনি তোমরা। বাইরে এমন কিছু থাকতে পারে যা তোমাদের ব্যথা দেবে, কষ্ট দেবে আমাকেও। তাই আমার কথা না শুনলে বিপদে পড়তে হবে।’
চুপ করে থাকল দু’জন।
‘বুঝতে পেরেছ আমার কথা?’
‘হ্যাঁ।’
‘হ্যাঁ।’
যাক, প্রশিক্ষণ শেষ। এবার কাজে নামার পালা।
‘ঠিক আছে,’ ম্যালরির কণ্ঠে উত্তেজনা। ‘আমরা এখন রওনা দেব। এখনই। চলে যাচ্ছি আমরা।’
বাচ্চাদের মাথা নিজে কপালে আঁকড়ে ধরল ও। তারপর হাত ধরে রওনা দিল বাইরে।
কিচেন পর্যন্ত এসে গাল থেকে পানির শেষ ফোঁটাগুলো মুছল ম্যালরি। কাঁপতে কাঁপতে পট্টি বাঁধল নিজের চোখে। সব শেষে হাত রাখল ডোরনবে। গত কয়েক বছরে এই দরজা পেরিয়ে কুয়া থেকে হাজার হাজার বালতি পানি টেনে এনেছে বাড়ির ভেতর।
আজ সব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রূঢ় বাস্তবতা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে হৃদয়কে।
দরজা খোলার সাথে সাথে ঠাণ্ডা বাতাস গা ছুঁয়ে দিল। বাইরে পা রাখল ম্যালরি। ভয় ভয় লাগছে বুকের ভেতর। তবে বাচ্চাদের সামনে এই অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে না। এই প্রভাব পড়ল মুখ দিয়ে বের হওয়া কথায়। প্রায় চিৎকারের শামিল।
‘আমার হাত ধরে রাখো। দু’জনেই।’
ছেলেটা ম্যালরির বাম হাত ধরল। মেয়েটার ছোট ছোট আঙুল আঁকড়ে ধরল ডান হাত।
চোখ বাঁধা অবস্থায় যাত্রা শুরু করল তিনজন।
কুয়াটা বিশ কদম সামনে। ছবির ফ্রেম ভেঙে বের করা ছোট ছোট কাঠের টুকরো পথনির্দেশ করছে। এগুলো অনুভব করে করে দিকনির্ণয় করতে হবে। পথের দু’পাশে পুঁতে রাখা কাঠগুলো আগেও অনেকবার জুতো দিয়ে অনুভব করেছে বাচ্চারা। ম্যালরি একবার ওদের বলেছিল, কুয়ার পানি হচ্ছে সর্বরোগের মহৌষধ। এতে করে জায়গাটার প্রতি অন্যরকম একটা ভক্তি আসে ওদের। তাই পানি নিতে মা-কে সাহায্য করায় কখনও ক্লান্ত হয়নি কেউ।
কুয়ার পর থেকে পায়ের নিচে এবড়োখেবড়ো মাটি ঠেকল। কেমন যেন অপ্রাকৃত সব, অতিরিক্ত নরম।
‘এই যে এদিকে,’ ম্যালরি বলল।
সাবধানে বাচ্চাদের নিয়ে আগে বাড়ল তারপর। কুয়া থেকে দশ গজ সামনে আরেকটা পথের শুরু। দুই পাশে গাছের সারি। এখান থেকে নদী একশো কদমও হবে না। বাচ্চাদের হাত ছেড়ে পথের নাগাল পাওয়ার জন্য হাতড়াল ম্যালরি।
‘আমার কোট ধরে রাখো!’
ডালপালা হাতড়ে একটা ট্যাংক টপ খুঁজে পেল ও। গাছের সাথে বেঁধে রাখা। রাস্তা বদলানোর চিহ্ন। তিন বছরের বেশি সময় ধরে এখানে ঝুলছে কাপড়টা।
ছেলেটা ম্যালরির পকেটের ঝুল আঁকড়ে ধরে রেখেছে, মেয়েটা ধরেছে ওর হাত। হাঁটতে শুরু করল সবাই। একটু পরপর ম্যালরি প্রশ্ন করছে, ওরা ঠিকমতো পরস্পরকে ধরে রেখেছে কি না। হঠাৎ মুখে গাছের ডালের খোঁচা লাগল। চিৎকার আটকাতে বেগ পেতে হলো ওকে।
কিছুক্ষণের মধ্যে পরের চিহ্নের কাছে পৌঁছে গেল ছোট দলটা। কিচেন চেয়ারের একটা ভাঙা পা, দাঁড়িয়ে আছে একদম পথের মাখখানে। ম্যালরির লাথি লেগে উল্টে পড়ল জিনিসটা।
চার বছর আগে নৌকাটা আবিষ্কার করে ম্যালরি। নিজেদের বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচ বাড়ি পরে নোঙর করা অবস্থায়। এক মাসের বেশি হয় এখানে পরীক্ষা করতে আসা হয়নি। তবে ও আশা করছে জিনিসটা জায়গামতোই আছে।
কিন্তু যদি না থাকে? যদি অন্য কেউ নিয়ে যায়? তাহলে কী হবে?
ঘাটে যাওয়ার আগেই আরাধ্য আওয়াজটা ম্যালরির কানে এল। পানিতে দুলছে নৌকাটা। থেমে বাচ্চাদের চোখের পট্টিতে হাত বুলাল ও। শক্ত করে দিল গিঁট। তারপর এগোল কাঠের জেটির দিকে।
হ্যাঁ, আছে ওটা। বাড়ির বাইরে অকেজো গাড়িগুলো যেমন বছরের পর বছর ধরে পড়া, তেমনিভাবে নিজের অবস্থানে টিকে আছে এই বাহনটাও।
বারি থেকে এত দূরে ঠাণ্ডার প্রকোপ বেশি। পানির ছল-ছলাৎ আওয়াজ মনে ভয় সঞ্চার করছে। উবু হয়ে নৌকার স্টিলের আগার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াল ম্যালরি। বাচ্চাদের হাত ছেড়ে দিয়েছে আগেই। সবার আগে দড়ির নাগাল পাওয়া গেল।
‘ছেলে,’ নৌকার বরফ শীতল ধাতব মাথা ধরে ঘাটের দিকে টানল ম্যালরি। ‘সামনে, সামনে উঠে পড়ো।’ বলে নিজেও সাহায্য করল উঠতে। স্থির হয়ে বসানোর পর বাচ্চাটার মুখ স্পর্শ করল দুই হাতে। ‘শুনতে থাকো। পানির দিকে কান রাখবে। ভুল যেন না হয়।’
মেয়েটাকে ঘাটে থাকতে বলে হাতড়ে হাতড়ে দড়ির বাঁধন খুলল ম্যালরি। তারপর সাবধানে উঠল মাঝের বেঞ্চে। সব শেষে বাচ্চাটাকেও উঠতে সাহায্য করল। পাগলের মতো দুলছে ওদের বাহন। অস্ফূট কণ্ঠে আঁতকে উঠল মেয়েটা। আঁকড়ে ধরেছে মায়ের হাত।
নৌকার নিচে পাতা, কাঠি ইত্যাদি হরেক রকম আবর্জনা জমেছে। কিছুটা পানিও আছে। সবকিছুর মাঝে হাত চালিয়ে ম্যালরি বৈঠাগুলো খুঁজে নিল। ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে কাঠের হাতল। ছত্রাকের গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাত্তা না দিয়ে ওগুলো তুলে নিল ম্যালরি, বসাল স্টিলের খাঁজে। এখনও যথেষ্ট মজবুত। একটা দিয়ে ঘাটে ধাক্কা দিল ও…
নেমে এল নদীতে।
পানি মোটামুটি শান্ত। জঙ্গলের দিক থেকে অস্ফূট আওয়াজ হঠাৎ ওদের পিলে চমকে দিল। কী যেন নড়ে উঠেছে ওদিকে।
কুয়াশার কথা ভাবল ম্যালরি। আশা করছে, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পালাতে পারবে।
কিন্তু ক্রমশ সরে যাবে কুয়াশা।
‘বাচ্চারা,’ বড় করে দম নিল ম্যালরি। ‘শুনতে থাকো।’
অবশেষে চার বছরের অপেক্ষা, প্রশিক্ষণ, আর জমা করা সাহসের উপর ভর করে বৈঠায় জোর খাটাল ও। পানি কেটে নৌকা এগোতে শুরু করেছে। দূরে সরে যাচ্ছে নদীর তীর, পেছনে পড়ছে বাড়ি। খুব বেশিদিন এই বাড়িতে থাকেনি ওরা, মাত্র চার বছর… কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে ছিল এখানেই।
-Josh Malerman
Translated by Adnan Ahmed Rizon
Published by Adee Prokashon